সাহিত্য, শিল্প, অথবা সংগীত- যেটার কথাই বলা হোক না কেন; এইসব সৃষ্টি-কৃষ্টি (বা অনেকের ভাষায় পরিবেশনগত সংস্কৃতি)-এর মূলে আছে মানবিক সৃজনশীলতা। বাংলার শতাব্দী-প্রাচীন সভ্যতা আর ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে আছে সৃজনশীলতার ভিত্তিতেই। বৈচিত্র্যময় বাংলায় একদিকে লোকশিল্পের শেকড় হয়েছে দৃঢ় ও বিস্তৃত; ঐকতান তুলেছে আঞ্চলিক মিশ্রণের; অন্যদিকে আধুনিক সাহিত্যের বহুমাত্রিক রূপসমৃদ্ধ হয়েছে।
সাম্প্রতিককালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রযাত্রা এই ধারাবাহিকতায় যোগ করছে নতুন এক মাত্রা। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় যেমন সৃজনশীলতা নতুন দিগন্ত খুঁজে পাচ্ছে, তেমনি মৌলিক শিল্প-সাহিত্য, লোকজ সংস্কৃতি এমনকি হস্তশিল্পও হচ্ছে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।
কবি হবার অভিপ্রায়
সাহিত্য বরাবরই ভাষার স্বতন্ত্রতা ও সৃষ্টিশীলতার ওপর নির্ভরশীল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবধারা থেকে শুরু করে সত্তরের দশকের আধুনিক কবিতা— সবকিছুর মধ্যেই ভাষার এক নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে। প্রকাশের সাবলীলতা আর ভাষার প্রাঞ্জলতা আরও বিকশিত হয়েছে হুমায়ূন আহমেদের হাতে। আর সর্বদা সদ্যজাত কবিতা লিখেছেন জীবনানন্দ দাশ। সমকালীন আর চির-প্রাসঙ্গিক কবি-সাহিত্যিকদের তালিকা দীর্ঘ হয়েছে তাদের সৃজনশীলতার ওপর ভিত্তি করে।
সমসাময়িককালে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে লেখা যাচ্ছে গল্প, কবিতা এমনকি উপন্যাসও। আর অনুবাদের ক্ষেত্রে হর-হামেশা ব্যবহার হচ্ছে চ্যাট-জিপিটি সহ অনেক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর প্রোগ্রাম। এমনকি ছন্দ আর মাত্রা মানিয়ে চলে কবিতা বেশ ভালই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রোগ্রামগুলো। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই প্রযুক্তির প্রভাব দেখা যাচ্ছে।
তবে কি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের সৃজনশীলতাকে প্রতিস্থাপন করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে বোঝা যায়, সাহিত্য মূলত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ। যেকোনও কবিতা বা গল্পের মূল চালিকা শক্তি লেখকের মানসিক আবেগ ও সমাজ-রাজনীতির প্রতিফলন। একথা সত্যি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভাষার কাঠামো ও শব্দচয়ন অনুকরণ করতে পারে; কিন্তু তার ভেতরে সেই অনুভূতি বা জীবনবোধের গভীরতা থাকে না।
বিশ্বব্যাপী একাধিক গবেষণা দেখিয়েছে যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে রচিত সাহিত্য পাঠকের কাছে মুগ্ধতা তৈরি করতে পারে, তবে তা গভীর মানবিক বোধের প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের এক গবেষণায় দেখা গেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় রচিত সাহিত্য টেকনিক্যালি নিখুঁত হলেও মানবিক আবেগ ও সৃজনশীল গভীরতার ক্ষেত্রে তা এখনও পিছিয়ে আছে। গবেষক নিনা বেগুসের নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-লিখিত গল্প ও কবিতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়, যেখানে পাঠকেরা মানবসৃষ্ট সাহিত্যের আবেগ ও বৈচিত্র্যকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন।
বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় যখন সাহিত্যিক চরিত্র সৃষ্টির প্রসঙ্গে আসা যায়। বাংলা সাহিত্যের আইকনিক চরিত্র দেবদাস থেকে হিমু, অথবা মিসির আলি কিংবা ফেলুদা —এদের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে লেখকের জীবন অভিজ্ঞতা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও দর্শনের মিশ্রণে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি নিখুঁত চরিত্র নির্মাণ করতে পারবে, কিন্তু সেই চরিত্রে মানবিক জটিলতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতা কতটা থাকবে? যন্ত্র কি পারবে জীবনানন্দ দাশের বিষন্নতা, ফররুখ আহমেদের দ্রোহ, কিংবা নজরুলের বিদ্রোহী সত্তাকে অনুভব করতে?
সুর-ছবির যন্ত্রযুগ
লোকগান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি এবং আধুনিক গান; সব মিলেই বাংলার সঙ্গীতাঙ্গন। তবে বিশ্বব্যাপী সংগীতশিল্পে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ব্যাপকভাবে বাড়ছে, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুর তৈরি করা হচ্ছে, এমনকি কৃত্রিম কণ্ঠ ব্যবহার করে নতুন গান প্রকাশ করা হচ্ছে। অডিও বিশ্লেষণ-ভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি গানের নির্দিষ্ট ধারাকে অনুসরণ করে নতুন সুর তৈরি করতে পারে, যা বাজার-কেন্দ্রিক গান তৈরির ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতে সুর-সৃষ্টির মৌলিকতা কোথাও হারিয়ে যাচ্ছে।
চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন, বছর-খানেক আগে সিনেলাইটিক নামের এক স্টার্ট-আপের সঙ্গে চুক্তি করে “ওয়ার্নার ব্রাদার্স”-এর মতো শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। চুক্তি অনুযায়ী কোনও চলচ্চিত্র নির্মাণের দায়িত্ব নেবে কিনা, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ওয়ার্নার ব্রাদার্সকে সাহায্য করবে সিনেলাইটিকের অ্যালগরিদম। হলিউড বা বলিউডের মতো বাংলাদেশেও চলচ্চিত্র নির্মাণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিশেষত ভিএফএক্স ও অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে খরচ কমছে এবং প্রোডাকশন সহজ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে প্রচলিত চলচ্চিত্র নির্মাণশৈলী ও সৃজনশীলতার উপর কী প্রভাব পড়বে, তা ভাবনার বিষয়।
উল্লেখ্য, দেশেই সম্প্রতি চলচ্চিত্র শিক্ষক ও নির্মাতা রাজীবুল হোসেন ২০০৬ সালে তার নির্মিত ডিজিটাল চলচ্চিত্র ‘বালুঘড়ি’ রি-মাস্টারিং করেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায়। এমনকি এই চলচ্চিত্রের একটি গানের কথা, সুর ও সংগীতায়োজন সবকিছুতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করেন তিনি।
চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির প্রভাব সুস্পষ্ট। এখন ডিজিটাল আর্টের প্রসার ঘটছে, এমনকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শিল্পকর্ম তৈরি করা হচ্ছে। এটি সৃজনশীলতাকে নতুন মাত্রা দিলেও, হাতে আঁকা শিল্পের বিশেষত্বকে হুমকির মুখে ফেলছে। যেমন, বাংলাদেশের রিকশা পেইন্টিং, নকশিকাঁথা বা জামদানির মতো শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর হাতে তৈরি নৈপুণ্যের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কিন্তু যন্ত্র-নির্ভর ডিজাইনের পাশাপাশি এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে নকশা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, যা শিল্পীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে ‘মেশিন জামদানি’ আরেকটি বড় উদাহরণ। জামদানি মূলত হাতে তৈরি হওয়ায় প্রতিটি নকশার মধ্যে থাকে শিল্পীর নিজস্বতা। কিন্তু এখন ডিজিটাল প্রযুক্তি ও আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহারে জামদানির নকশা সহজেই পুনরুৎপাদিত হচ্ছে, যা দ্রুত উৎপাদন সম্ভব।
আগলে ধরতে ইতিহাস
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সৃজনশীল সংস্কৃতির কিছু ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে, তবে এটি ঐতিহ্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তাদের সংগ্রহসমূহ ডিজিটালাইজেশন ও তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ করছে। ২০১০-২০১২ সালে ‘বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তথ্য যোগাযোগ ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জাতীয় জাদুঘর তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো নির্মাণ করে, এবং বর্তমানে অনেক কিছুই তারা ডিজিটালি সংরক্ষণ করছে।
এছাড়া বাংলা সাহিত্যের পুরনো গ্রন্থাবলী ও পুঁথিসমূহের ডিজিটাল রূপান্তরও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সহজতর হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় অক্ষর চেনার (OCR) প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পুরনো হাতে লেখা গ্রন্থগুলোর পাঠোদ্ধার ও সংরক্ষণ সহজ হয়েছে। এছাড়া, বাংলা ভাষার কথ্য রূপ ও আঞ্চলিক ভাষাগুলোকেও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চলছে, যা ভবিষ্যতে ভাষার বিবর্তন বুঝতে গবেষকদের সাহায্য করবে।
বাংলা ভাষার সংরক্ষণ ও প্রমিতকরণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। “হাতেকলমে ‘বাংলা’ ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং” বইটি বাংলা ভাষার প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করে, যা বাংলা ভাষার ডাটাবেজ তৈরি ও ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণে সহায়তা করছে।
এইভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধুমাত্র নতুন সৃজনশীলতার সুযোগ সৃষ্টি করছে না, বরং অতীতের সাহিত্য, ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংরক্ষণ করেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি মূল্যবান ভাণ্ডার তৈরি করছে।
উপসংহার:
প্রতিটি শিল্পবিপ্লব মানুষের সৃজনশীলতায় পরিবর্তন এনেছে, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর চতুর্থ শিল্পবিপ্লবও তার ব্যতিক্রম নয়। একসময় মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার যেমন সাহিত্যের প্রসার ঘটিয়েছিল, তেমনি ডিজিটাল প্রযুক্তি বর্তমানে সৃজনশীল কাজের পরিধি ও গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সৃজনশীলতার জন্য একদিকে সুযোগ তৈরি করছে, অন্যদিকে মৌলিক সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করছে।
প্রযুক্তির এই অগ্রযাত্রা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য। একদিকে, এটি ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসারে সাহায্য করছে, অন্যদিকে সৃজনশীলতার ওপর প্রভাব ফেলছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর অনুবাদ ব্যবস্থা, স্বয়ংক্রিয় লেখনী, এবং সাহিত্য বিশ্লেষণের মতো নতুন প্রযুক্তি বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখছে।
তবে প্রশ্ন থেকে যায়— এই প্রযুক্তির মাধ্যমে রচিত সাহিত্য বা শিল্প কি মানবিক অনুভূতির গভীরতা ধারণ করতে পারবে?
ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি আরও উন্নত হবে, এবং সেই সময় প্রশ্ন উঠবে— আমরা কি প্রযুক্তির আধিপত্যে নিজেদের সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলব, নাকি মানবিক আবেগ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাব? এর উত্তর খুঁজে পাওয়া আমাদের ভবিষ্যতের শিল্প ও সাহিত্য ব্যবস্থার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
পুনশ্চ: এই প্রবন্ধের বেশ কিছু অংশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় (chat-gpt, gemini, deep seek) লেখা।
লেখক: ব্লগার ও আইটি প্রফেশনাল; যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস ফোরাম।
%e0%a6%95%e0%a7%83%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ae-%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a7%e0%a6%bf%e0%a6%ae%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%ac%e0%a6%a6%e0%a7%8c










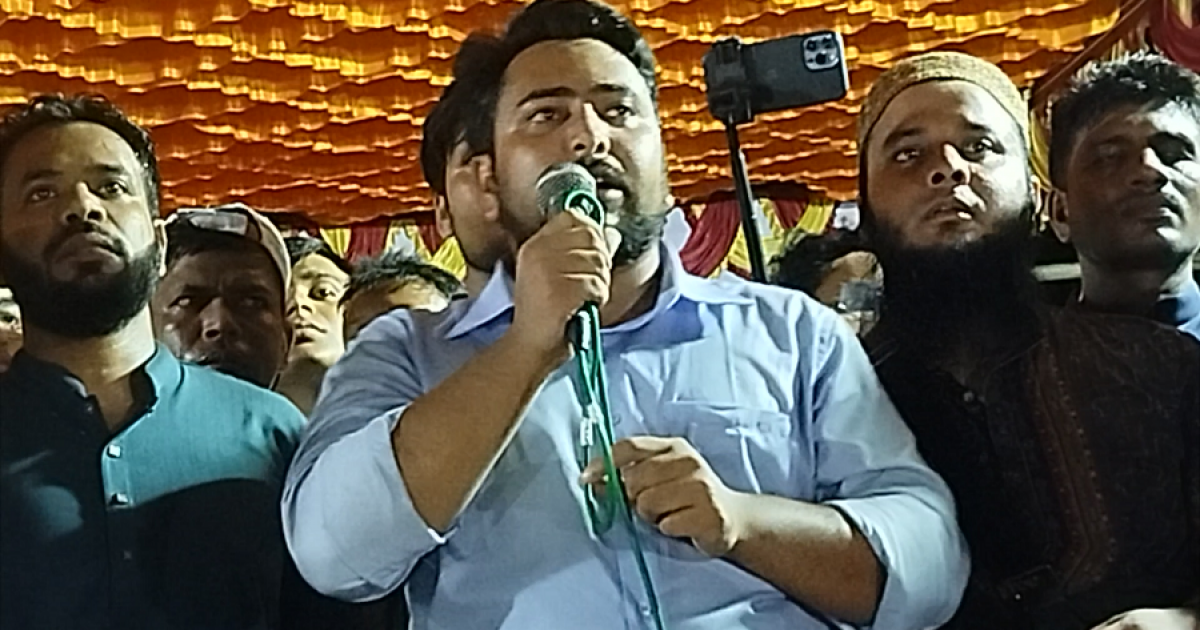




Leave a Reply